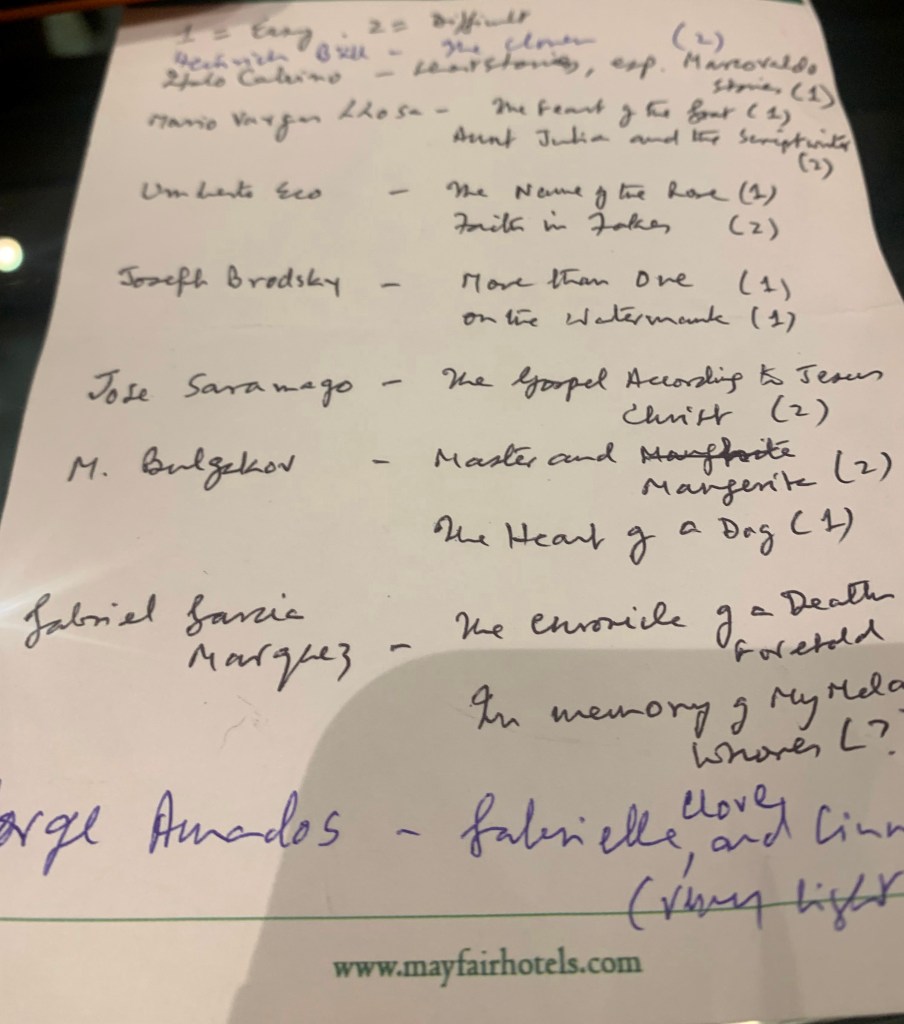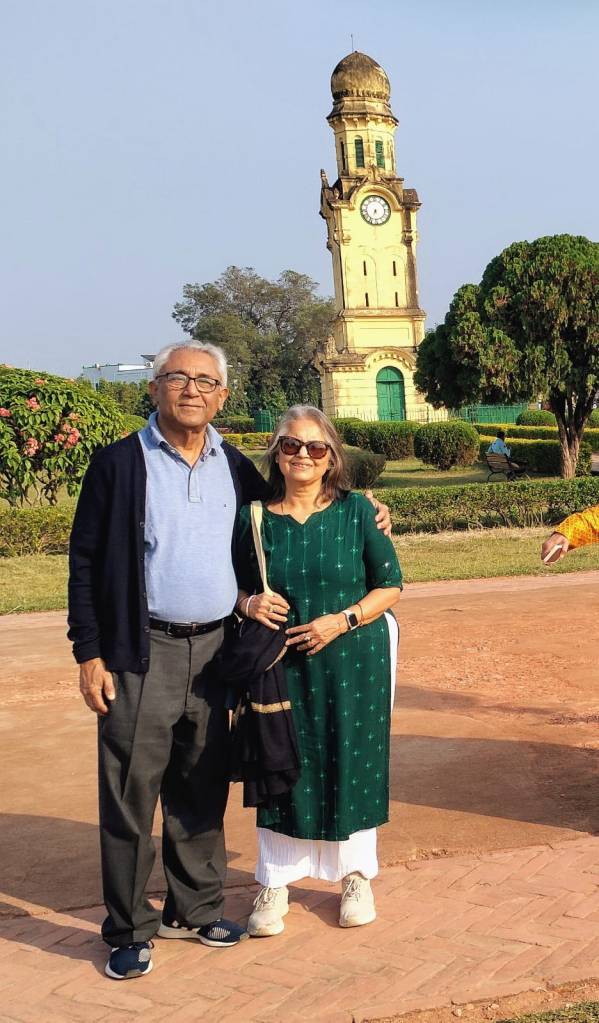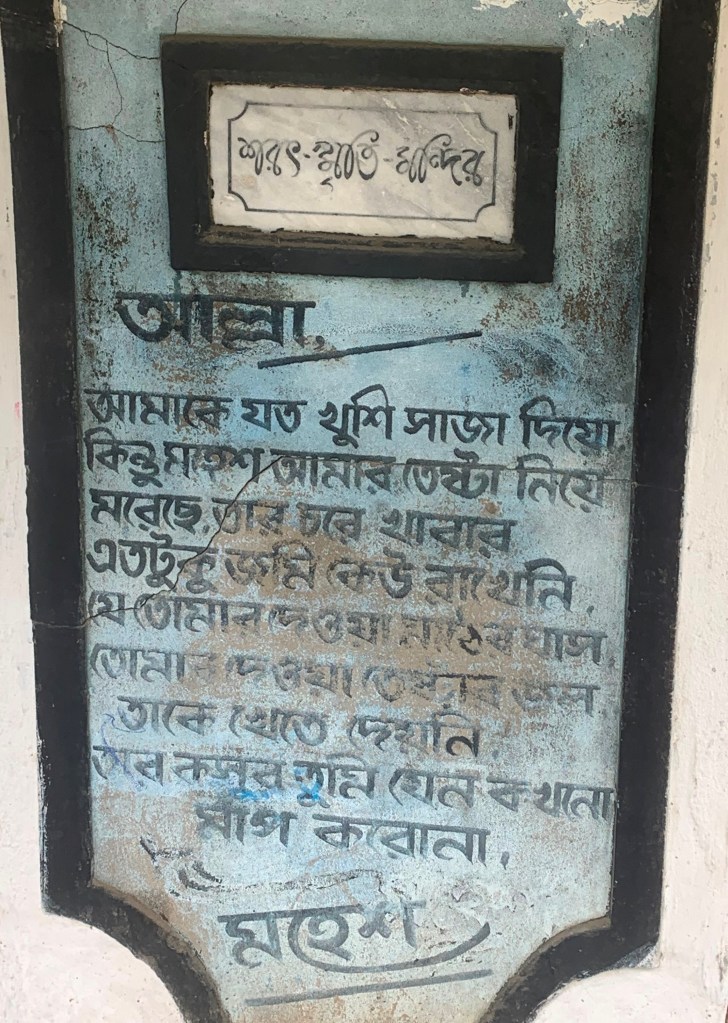১) পূর্ব্বকথা
কথায় আছে বাবা বিশ্বনাথ না ডাকলে কাশী যাওয়া হয়না।
ছোটবেলায় মা’র সাথে প্রতি বছর দিদার কাছে কাশী আসতাম। শেষ এসেছিলাম ১৯৬৫ সালে বাবার মৃত্যুর পরে, তখন খড়্গপুরে কলেজে পড়ি, গরমের ছুটিতে। তার পর অনেক বছর কেটে গেছে। বাবা বিশ্বনাথ আমায় ডাকেননি, আমারও আর কাশী আসা হয়নি।
২০১৯ সালে আমার শ্বাশুড়ী আর মা পর পর জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী মাসে চলে গেলেন। তাঁদের দু’জনের বাৎসরিক কাজ করার কথা এক বছর পরে ২০২০ সালে, সেই কাজ ঠাকুরমশায়কে ডেকে বাড়ীতে করানো হলো। তখন কোভিড অতিমারী চলছে, লকডাউনের সময়ে তাঁদের আত্মাকে পিন্ডদান করতে গয়া বা কাশী যেতে পারিনি।
এবার ২০২৪ সালের মার্চ মাসে শেষ পর্য্যন্ত বাবা বিশ্বনাথের ডাক এলো।
আমরা আমার শ্বাশুড়ী আর মা’র পিন্ডদান করতে কাশী এসেছি। আমাদের সাথে এসেছে আমাদের বড় মেয়ে পুপু। সে লন্ডনে ডাক্তার। ঠাম্মা আর দিদিভাইকে সে খুব ভালোবাসতো, তাই সে ছুটি নিয়ে আমাদের সাথে তাঁদের আত্মাকে পিন্ডদান করা দেখতে কাশী এসেছে, এই সুযোগে তার কাশী দেখা হয়ে যাবে। বাবা বিশ্বনাথ আমাদের সাথে তাকেও ডেকে নিয়েছেন।
ভারত সেবাশ্রম সংঘে পিন্ডদান হবে, আগে থেকেই ফোন করে সব বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে। পুরোহিত মশাইয়ের নাম ছোটু মহারাজ, তিনি সব জিনিষ যোগাড় করে রাখবেন, আমাদের কেবল এসে পুজোর কাজটা করতে হবে। আমি মা’র কাজ করবো, সুভদ্রা করবে আমার শ্বাশুড়ীর কাজ।
১৯৬৫ সালের পরে ২০২৪, অর্থাৎ প্রায় ষাট বছর I পরে আমি কাশী এলাম।
এই ষাট বছরে কাশী অনেক পালটে গেছে, আর আমিও এখন সেই আগেকার শিশু বা কিশোর নই। আমার নতুন চোখে এই নতুন কাশীকে কেমন দেখবো, তাই নিয়ে মনে মনে প্রথম থেকেই আমি বেশ একটা আগ্রহ অনুভব করছিলাম।
তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ/
বসন্ত সে রঙ্গীন বেশে ধরায় তখন অবতীর্ণ।
আর এখন আমার অবস্থা হলো “বসন্ত সে কবেই গেছে, শরীর এখন জরাজীর্ণ।”
কাশী কিছুটা আমার সেই বাল্য কৈশোর আর আজকের বার্ধক্যের মধ্যে একটা সেতুর মতো।
এটা হলো সেই সেতুবন্ধের গল্প।




২) ষাট বছর পর প্রথম কাশী দর্শন
এই প্রথম প্লেনে কাশী এলাম। পুপু এলো দিল্লী থেকে। ওর ফ্লাইট কিছুক্ষন আগে এসেছে, আমাদের জন্যে সে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল।
ছোটবেলায় তো প্লেনে ওঠার সামর্থ্য আমাদের ছিলনা, মা’র সাথে ট্রেণে কাশী আসতাম। ট্রেণে কাশী যাবার একটা প্রধান স্মৃতি ছিল বেনারস স্টেশনের ঠিক আগে গঙ্গার ওপরে লম্বা ব্রীজ। সেই ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেণ যাবার সময়, ট্রেণের ভিতর থেকে একটা সমবেত কন্ঠে “গঙ্গা মাইকি জয়” রব উঠতো। তাছাড়া প্রায় সবাই তাদের গঙ্গা মাই কে প্রণামী হিসেব নদীর জলে পয়সা ছুঁড়তেন, এবং সেগুলো ব্রীজের গার্ডারে লেগে ঝনঝন একটা শব্দ হতো, সেই শব্দ এখনো কানে বাজে।
ট্রেণের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম বহু দূরে কাশীর গঙ্গার তীরের ইঁট রং এর উঁচু উঁচু বাড়ীগুলো, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে সিঁড়ি নেমে গেছে নদীতে। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে ভোলা প্রায় অসম্ভব। সত্যজিৎ রায় তাঁর “অপরাজিত” সিনেমার শুরুতেই ব্রীজের ওপর ট্রেণ থেকে দেখা কাশীর ঘাটের ওই দৃশ্যটা ব্যবহার করেছেন।
স্টেশন থেকে নেমে আমরা সাইকেল রিক্সা অথবা ঘোড়ায় টানা গাড়ী (টাঙ্গা) চড়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে দিদার বাড়ীতে পৌঁছে যেতাম। পথে শহরের নানা দৃশ্য চোখে পড়তো। সেই সব দৃশ্য এখন সাদা কালো ছবির মতো শুধু আমার মনে।
ষাট বছর পরের এই শহর এখন কেমন লাগবে আমার চোখে?
বেনারস এয়ারপোর্টটা বেশ বড় আর সাজানো গোছানো। সিঁড়ি দিয়ে হলে নেমে আসতেই দেখি সামনে পুপু আমাদের জন্যে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। আমাদের মালপত্র নিয়ে আমরা বেরোলাম। বাইরে তখন বিকেলের উজ্জ্বল আলো।
হোটেলের ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে এসেছে, বেশ আরামাদায়ক বড় গাড়ী (SUV), আমরা সেই গাড়ীতে উঠে হোটেলের দিকে চললাম।
আমাদের ড্রাইভার এর নাম ভোলা। কাশীতে সবার নামই মহাদেব এর নামে হবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে? ভোলা ফোনে কার সাথে কথা বলছে, ভোজপুরী ভাষায় নাকি? জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো কাশী শহর বিহার এর বর্ডার এর খুব কাছে। আর বর্ডারের ওপারেই ভোজপুর জেলা, তাই কাশীতে ভোজপুরী ভাষা খুব প্রচলিত, এই ভাষায় এখানে অনেকেই কথা বলে।
কাশী শহর এয়ারপোর্ট থেকে অনেকটা দূর, যেতে সময় লাগলো ঘন্টা খানেক। যেতে যেতে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখছিলাম – তখন বিকেলের রোদ এসে পড়েছে দু’দিকের ছোট ছোট বাড়ীতে, চারিদিকে খোলামেলা সবুজ, দেখে মনে হয় বেশ বর্দ্ধিষ্ণু জায়গা। কিন্তু ক্রমশঃ যত শহর কাছে আসতে লাগলো ততো ঘড়বাড়ী দোকানপাট আর সাইকেল অটো আর মানুষের ভীড় বাড়তে লাগল।
সেই পড়ন্ত বিকেলে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলের দিকে যেতে যেতে বেনারস শহরের ব্যস্ত রাস্তা দেখছিলাম, নানা দৃশ্য চোখে পড়ছিল, রাস্তার দুই পাশে বেনারসী শাড়ীর দোকান, চারিদিকে হিন্দী সাইনবোর্ড, অটো রিকশা আর পথচারীদের ভীড়। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে কাশীর বিখ্যাত সরু সরু গলি। কালো বোরখা পরা কিছু কিশোরী দলবেঁধে হেসে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, হয়তো তারা স্কুল থেকে ফিরছে।
দেখতে দেখতে ভাবছিলাম কত প্রাচীন এই বারাণসী শহর, হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ। স্বয়ং শিব এখানে এসে ভিক্ষা নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণার কাছ থেকে। এই শহর মুসলমানদের অধীনেও থেকেছে, মন্দিরের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে মসজিদ। ফলে এখানে হিন্দু ও মুসলমান নারী পুরুষ যত্রতত্র দেখা যায়।
সারা বিশ্বে আমাদের হিন্দুদের মোট সাতটি পবিত্র ভূমি রয়েছে, যেখানে গেলে মানুষ মোক্ষ লাভ করতে পারে। অযোধ্যা, মথুরা, গয়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারবতী – এই সাতটি শহরকে একত্রে বলা হয় সপ্তপুরী। কাশী এই সপ্তপুরীর অন্যতম পবিত্র ভূমি। পাশাপাশি এই শহরটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গা নদীতে স্নান করা হিন্দু ধর্মমতে বিশেষ পুণ্যের কাজ।
কাশীর গঙ্গায় স্নান করে বিশ্বনাথ দর্শন করলে পার্থিব জীবনের যত জ্বালা আর যন্ত্রণা থেকে চিরকালের জন্যে নিশ্চিত মুক্তি এই বিশ্বাস থেকে দলে দলে হিন্দুরা যুগে যুগে সারা দেশ থেকে মন্দিরে শিবের দর্শন করতে ও পূজো দিতে আসেন।
এই বিশ্বাস থেকে আমার দিদিমা ও তাঁর শেষ জীবনে বেশ কয়েক বছর কাশীতে একা একা থেকেছেন। মা মামা মাসীরা অবশ্য তাঁকে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে নিজেদের কাছে নিয়ে এসে রাখেন।
আমার বার্ধক্যে আমি অবশ্য নিজের জন্যে কোন পুণ্য অর্জ্জন করার জন্যে কাশী আসিনি। আমি এসেছি আমার মা’র পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে। আমার মা রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে বড় হয়েছেন, সারা জীবন নিষ্ঠার সাথে পুজো আর্চা এবং শিবরাত্রি বা কালীপূজোতে নির্জলা উপোস এই সব করেছেন। আমার বাবার মৃত্যুর পরে তিনি আমায় নিয়ে গয়া গিয়েছিলেন, সেখানে আমরা তাঁর পারলৌকিক আত্মার শান্তির জন্যে তাঁকে পিন্ডদান করেছিলাম।
সুতরাং তিনি নিশ্চয় চেয়েছিলেন যে তাঁর একমাত্র সন্তান তাঁর মৃত্যুর পরে পিন্ডদান করে তাঁর আত্মাকে মুক্তি দেবে। সেই কাজ করতেই আমার কাশী আসা। মা’র প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করাও অবশ্যই একটা পুণ্যের কাজ। তাছাড়া গঙ্গায় স্নান না করলেও বিশ্বনাথের দর্শন তো অন্ততঃ হবে।
প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল মা পরলোকে যাত্রা করেছেন, ঠিক এক বছর পরে ২০২০ সালে কোভিড অতিমারীর মধ্যে বাড়ীতে পূজো করে তাঁকে পিন্ডদান করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী গয়া কাশী হরিদ্বার এর মত তীর্থক্ষেত্র থেকে পিন্ডদান না করলে প্রেতাত্মা বৈতরণী নদীর ঘাটে অপেক্ষায় থাকেন, যতক্ষন না সন্তান পিন্ডদান করে ততদিন সেই নদী পেরিয়ে তাঁর প্রেতাত্মার স্বর্গে প্রবেশ করার অনুমতি নেই।
এই সব ভাবতে ভাবতে আমাদের গাড়ী এক জায়গায় এসে একটা সরু গলির মুখে এসে দাঁড়ালো।
আমাদের হোটেলটা একটু ভেতরে নদীর ধারে, সেখানে গাড়ী যাবেনা , তাই হোটেলের দুই জন ইউনিফর্ম পরা লোক এসেছে তারা আমাদের মালপত্র নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দেবে। হেঁটে মাত্র দুই বা তিন মিনিটের রাস্তা, একটু এগোতেই হোটেলে পৌঁছে গেলাম। পাশেই শিবালা ঘাট, নদীর দর্শন পেলাম। নিজের মনে বয়ে চলেছে পুণ্যসলিলা গঙ্গা। এখানে জলের রং নীল, কলকাতার মত পলিমাটিতে ভরা হলুদ রং নয়। দেখে মনটা বেশ ভাল হয়ে গেল।
আমাদের হোটেলের নাম সূর্যোদয় হাভেলি, এই হোটেলটি আগে রাজস্থানের কোন মহারাজের বাড়ী ছিল শুনলাম। বেশ দামী হোটেল, শাকাহারী, অর্থাৎ এখানে সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার পরিবেশন করা হয়।
শুনেছি আধুনিক বারাণসীর বেশির ভাগটাই রাজপুত ও মারাঠা রাজাদের হাতে তৈরি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তৈরী এই শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাড়ীর বেশিরভাগই তাই। সেই সব রাজা রাজড়ারা বলা বাহুল্য শিবের ভক্ত ছিলেন। এবং তাঁদের তৈরী এই সব হাভেলিতে তাঁরা সপরিবারে এসে থাকতেন। কাশীতে গঙ্গার ধারে প্রাসাদোপম হাভেলি থাকা একরকমের আভিজাত্যের প্রকাশ, তাছাড়া পুণ্যও হয়।
এখন এই সব হাভেলির অনেকগুলোই হোটেল হিসেবে চালানো হয়। ছোটবেলায় যখন আসতাম, তখন কাশীতে এত হোটেল ছিলনা।






৩) কাশী আর বেনারস
কাশী আর বেনারস দুটো আলাদা রেলস্টেশন হলেও আসলে কিন্তু ওরা একই শহরের দুই নাম। পরে শুনেছি ওখানে দুই উপনদী বরুণা আর অসি গঙ্গায় মিশেছে তাই সেখান থেকেই সন্ধি করে শহরের নাম হয়েছে বারাণসী। সেখান থেকে বেনারস।
অনেকে বলে কাশী হলো বাঙালীর, আর বেনারস হলো সারা ভারতের।
একই শহরের ভিতর দুই আলাদা শহর, তাদের আলাদা রূপ, আলাদা পরিচয়। আমার এক বন্ধু সিদ্ধার্থ পাঁচ বছর কাশীতে থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। তার মতে কাশী ও বেনারস দু’টো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ।
কাশীতে বাঙালীর প্রতিপত্তি বেশী, বিধবাশ্রম, ভাতের হোটেল, আনন্দময়ী মা, গঙ্গার ঘাট আর সিঁড়ি, হরিহর সর্ব্বজয়া আর ছোট্ট অপু। বাংলা সাহিত্যের অনেক কালজয়ী উপন্যাসের নায়িকারা নির্বাসিত হয়ে কাশীবাসিনী হয়েছেন। সেই সব উপন্যাসের মধ্যে আছে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক, বিভূতিভুষনের দ্রবময়ীর কাশীবাস, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ। এমনকি রবীন্দ্রনাথও চোখের বালির বিনোদিনী কে কাশী পাঠিয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে লেখা “সেই সময়” উপন্যাসে বালবিধবা বিন্দুবাসিনীকে তখনকার সমাজের রীতি অনুযায়ী কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
কাশীর একটা গোটা এলাকাই বাঙালির। যার নাম বাঙালিটোলা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দিব্যি বাংলা বলে চলেছেন প্রবাসীরা। এখানে তিন হাজারের বেশি দুর্গাপুজো হয়। এককালে সংস্কৃত শেখার জন্য বহু বাঙালি পাড়ি দিতেন কাশী। একটা সময় ছিল যখন কাশীতে রীতিমতো শাসন করতেন বাঙালি সংস্কৃত পণ্ডিতরা।
অন্যদিকে বেনারস হলো ভারতীয় সংষ্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ পীঠস্থান। বেনারসী শাড়ী, রাবড়ী, জর্দ্দা পান, কচুরী, মুজরা, বাইজী দের নাচ গান, কবি সন্মেলন, বিসমিল্লা খাঁর অষ্টপ্রহর সানাই, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বেনারেস ঘরানা। অপরাধ জগতের মগনলাল মেঘরাজেরাও বেনারসের অতি ঘোর বাস্তব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সময় উপন্যাসে গঙ্গানারায়ন তার ছেলেবেলার বান্ধবী এবং বালবিধবা কাশীতে নির্বাসিতা বিন্দুবাসিনী কে কাশীতে এসে হন্যে হয়ে খুঁজেছিল। শেষ পর্য্যন্ত সে বিন্দুকে যখন সে খুঁজে পায়, সে তখন এইরকম একজন অপরাধ জগতের মানুষের রক্ষিতা। সে গঙ্গার কাছে ফিরে যেতে রাজী হয়না, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।
বারাণসীকে ভারতের প্রাচীনতম শহর বলে মনে করা হয়।
এই শহর হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র শহর হলেও বারাণসী বৌদ্ধ, জৈন আর শিখ ধর্মেরও অন্যতম পীঠস্থান।
৫২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বারাণসীর কাছে সারনাথে বুদ্ধ প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিসত্ত্ব লাভ করার পর গৌতম বুদ্ধ তা প্রচার করার জন্য পঞ্চভার্গব ভিক্ষুর সন্ধানে প্রথম এসে পৌঁছেছিলেন সারনাথে। পরে সম্রাট অশোক সারনাথের একটি মৃগদাবে একটি বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কাশী এলে সারনাথে সেই মন্দির দর্শন করতে পর্য্যটকরা দল বেঁধে যান্। মা মাসীদের সাথে ছোটবেলায় আমিও বেশ কয়েকবার গেছি।
৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে চীনা পর্যটক ফাহিয়েন এবং পরে হিউয়েন সাং বারাণসীতে এসেছিলেন। তাঁদের রচনা থেকে এই শহরের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়।
ভক্তিবাদী আন্দোলনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবীর। কবীরকে “পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী সন্ত কবি ও অতিন্দ্রীয়বাদী” বলা হয়। ১৫০৭ সালের শিবরাত্রি উৎসবের সময় গুরু নানক এই শহরে আসেন। তার এই বারাণসী সফর শিখধর্ম্ম প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
কিন্তু শুধু ধর্ম দিয়ে বারাণসী কে চেনা যাবেনা।
এই শহর শত শত বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্প ও শিক্ষার উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান হিসেবে তার পরিচয় বজায় রেখেছে।
তুলসীদাস তাঁর জীবনের সিংহভাগ এই শহরে কাটিয়েছেন। রামায়ণের ওপর লেখা তাঁর বিখ্যাত কাব্য রামচরিতমানস তিনি এখানেই রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুও হয় এই শহরে।
কিছুদিন আগে গৌতম চক্রবর্ত্তী আনন্দবাজারে বারাণসীর ছেলে মুনসী প্রেমচন্দের ১৯১৮ সালে প্রকাশিত সাড়া জাগানো উপন্যাস “সেবাসদন” নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনায় উঠে এসেছে বিংশ শতাব্দীর (প্রাক স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার পর) কাশীর সাংষ্কৃতিক পরিবেশ। সেবাসদন উপন্যাসের নায়িকা ব্রাম্ভনের মেয়ে সুমন। বিয়ের আগে পিতৃগৃহে সে নাচ আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছে।
বৃদ্ধ স্বামী কে ছেড়ে সে কাশীর মন্দিরে সাধু সন্তদের সামনে গান গায়, নাচে।
গৌতম লিখেছেন~
——————
নাচনেওয়ালী? মন্দিরের চাতালে সাধুসন্ত ও দর্শনার্থী দের ভীড়ে শিবলিঙ্গের সামনে নাচছে গল্পের নায়িকা সুমন। সে যদি খারাপ মেয়ে হয়, তাহলে সে মন্দিরে কি ভাবে নাচে? সাধু সন্তরা তার নাচ দেখে এত ধন্য ধন্য করে কেন?
————–
ঊর্দ্দু থেকে ইংরেজীতে সম্প্রতি অনূদিত হবার আগে কেউ জানতোনা সাধুদের আশ্রমে মন্দিরে উচ্চাঙ্গ নাচ গানের এই সংষ্কৃতির কথা। নানা অনুষ্ঠানে সরস্বতী পূজোর দিন, বাইজী, মুজরো গায়িকা এমন কি বহুবল্লভারা (ঊর্দ্দুতে “তওয়াইফ”রা) বিনা পারিশ্রমিকে দশাশ্বমেধ ঘাটে নাচ গান করতে আসতেন।
বারাণসীর ইমামবাদী বাইজীর কাছ থেকে গান শিখে প্রথম বাংলা টপ্পা গানের প্রচলন করেন নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। অঘোর চক্রবর্ত্তীর ধ্রুপদ বা মহেশচন্দ্র সরকারের মত বীণা বাদকের শিক্ষাও এই শহরে। কথক নাচ ও ছয় মাত্রার দাদরা তালের ও বিকাশ ঘটেছিল এই শহরে। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম সঙ্গীতকার তানসেনের বংশধরেরা অনেকেই বারাণসীকে তাদের বাসভূমি বলে বেছে নেন। তৈরী হয় বেনারস ঘরানা।
এঁদের কারুর মধ্যে ছিলনা ধর্ম বা জাত পাতের বিভেদ। কোন নোংরামীও ছিলনা, তবু স্বাধীনতার পরে সরকারের উদ্যোগে কাশীর ডালমন্ডির বাইজী মহল্লা তুলে দেওয়া হয়। যেহেতু এই তওয়াইফেরা অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান, তাই এই নিয়ে তখন খুব হৈ চৈ এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয় হয় পুরুষতন্ত্রেরই।
ডালমন্ডীর বাইজী প্রেমচন্দের উপন্যাসের নায়িকা সুমন বাইজী বা তওয়াইফ হলেও সে তার শরীরী সতীত্ব হারায়নি। উপন্যাসের শেষে তার স্বামীর সাথেও তার দেখা হয়।






৪) প্রথম সন্ধ্যা – দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গারতি
আমাদের ঘরটা বেশ বড়, পুপুর জন্যে একটা আলাদা বিছানার বন্দোবস্ত করতে অসুবিধে হইয়নি। বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের জন্যে একটা নৌকা বুক করা আছে, চেক ইন করে ঘরে মালপত্র রেখে আমরা সোজা ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠে বসলাম।
হোটেলটি তিনতলা। আমাদের ঘর এক তলায় হলেও নদী আরো অনেকটাই নীচে। ঘাটে যেতে সিঁড়ি বেয়ে তাই অনেকটা নামতে হলো। পাঁচটা বাজে কিন্তু তখনও বেশ আলো। দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গারতি দেখবো, সেখানে নৌকায় করে যেতে যেতে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছিলা। একের পর এক ঘাট পেরিয়ে যেতে থাকলাম, আর অনেকদিন পরে চোখে পড়লো কাশীর সেই পরিচিত দৃশ্য। সারি সারি উঁচু ইট রঙ এর বাড়ী আর জলে নেমে আসা সিঁড়ি।
ছোটবেলায় বাবা যখন কাশী আসতেন, তখন সবাই মিলে বিকেলে গঙ্গায় নৌকায় চড়ে অনেক দূরে চলে যেতাম। মাথার ওপরে নীল আকাশ, চারিদিকে নদীর নীল জল, মাঝির দাঁড়ের আওয়াজে জলে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ আসছে, আমি চলন্ত নৌকা থেকে জলে হাত নামিয়ে দিয়ে দেখতাম কেমন ঠাণ্ডা। মণিকর্ণিকা ঘাট এলে মা বলতেন এখানে চিতার আগুণ কখনো নেবেনা। কাশীতে অনেক মরণোন্মুখ মানুষ মারা যেতে আসেন, এই ঘাটে দাহ করলে মোক্ষলাভ হয়, আর পুনর্জন্ম হয়না।
এখন অবশ্য সবই ডিজেলে চালানো মটরবোট। চারিদিকে নদীতে মটরবোটের ছড়াছড়ি। এখানে আসার আগে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, কাশীর মশাদের কামড়ে নাকি ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়া হয়। আমরা প্রতিষেধক ক্রীম গায়ে আর জামায় মেখে নিলাম। সাবধানের মার নেই।
গঙ্গারতি নদী থেকেই দেখা হলো। দশাশ্বমেধ ঘাট তো লোকে লোকারণ্য, সামনে নদীতেও সারি সারি নৌকা, বড় বড় স্টীমার। তাতে ভর্ত্তি দর্শনার্থী ভক্তের দল। ক্রমশঃ অন্ধকার নেমে এলো, তার মধ্যে চারিদিকে জ্বলজ্বল করছে আলোর মালা। তার সাথে মাইকে শোনা যাচ্ছে ভজন আর স্তোত্রপাঠ। বেশ জমজমাট ব্যাপার।
গঙ্গারতি এখন গঙ্গার তীরে নানা শহরে হয়। এমন কি কলকাতায়ও। এক বছর আগে সুভদ্রা আর আমি হরিদ্বারে দেখেছি।




৪) দ্বিতীয় দিন
গতকাল আসা আর আগামীকাল ফেরার মাঝখানে আজ আমাদের কাশীতে একমাত্র দিন। সুতরাং এই দিনটিতে আমাদের প্রধান দুটি কাজ সারতে হবে, এক হলো মা’দের দু’জনের বাৎসরিক কাজ করা আর দুই হলো বিশ্বনাথ দর্শন। তারপরে বাকি সময়টা আমরা যতটা পারি কাশী শহরের অন্যান্য নানা দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়াবো।
ভোরে ব্যালকনি থেকে সূর্য্যোদয়
আমাদের ঘরের পাশে বাইরে একটা ছোট ব্যালকনি আছে, পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সেখানে তিন জনে চা খেতে খেতে সূর্য্যোদয় দেখা হলো। মন ভাল করা দৃশ্য। সেই ভোরেই ঘাটে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।
ব্যালকনি তে তিন জনে চা খেতে খেতে নদী দেখতে দেখতে আমার মন চলে যাচ্ছিলো সেই ছোটবেলার কাশীতে। রাণা মহলের বাড়ীর ছাতে গেলেই নীচে নদী দেখা যেতো, এখনকার মত তখনো পাশে চরে গাছগাছালি গজিয়ে উঠেছে। একটা ঘুড়ি ভোকাট্টা হয়ে দুলতে দুলতে ভেসে জলে গিয়ে পড়ছে। দূরে ব্রীজের ওপর দিয়ে গুম গুম আওয়াজ করে ট্রেণ চলে যাচ্ছে। এই সব নানা স্মৃতি।
আজও সেই একই দৃশ্য। কিছুই যেন বদলায়নি। দূরে চর, কাছে ঘাটে লোকে স্নান করছে, নদীর জলে এদিক থেকে ওদিক বোট আর নৌকারা ভেসে চলেছে, তাদের পিছনে পিছনে মাছের লোভে উড়ে যাচ্ছে অসংখ্য পাখীর ঝাঁক।
স্নান সেরে তৈরী হয়ে সকাল সকাল হোটেলেই ব্রেকফাস্ট। এখানে নিরামিষ খাবার খুবই সুস্বাদু। গতকাল কাল ডিনার ও এখানে করেছি। কাশীর কচুরী নাকি খুব বিখ্যাত, কিন্তু তা’ নাকি সকাল দশটার পরে আর কোন দোকানে পাওয়া যায়না। অদ্ভুত নিয়ম। আমাদের তাই আর কচুরী খাওয়া হলোনা।
কাশীতে ঘুরে বেড়াবার জন্যে গাড়ীর বদলে অটোই ভাল, কেননা সরু গলির মধ্যে গাড়ী ঢোকেনা অনেক দূরে পার্ক করে হাঁটতে হয়। হোটেল থেকেই একটি গাইড ছেলে কে কাল বলে রেখেছি, সে আজ সারাদিনের জন্যে একটা অটো ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।


কাশী বিশ্বনাথ মন্দির – ভাঙা আর গড়ার ইতিহাস
আমাদের প্রথম কাজ হলো বিশ্বনাথ দর্শন।
হিন্দুদের জন্যে কাশীর একটি প্রধান আকর্ষন হল কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। মন্দিরের ১৫.৫ মিটার উঁচু চূড়াটি সোনায় মোড়া। তাই মন্দিরটিকে স্বর্ণমন্দিরও বলা হয়ে থাকে।
যাই হোক, এই মন্দিরটি কবে প্রথম তৈরী হয়েছিল, তা নিয়ে নানা মতামত আছে। বারাণসীতে যে সবচেয়ে পুরনো পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে অনুমিত হয় গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই শহরে জনবসতি শুরু হয়েছিল খৃস্টপূর্ব একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীতে। এই জন্য বারাণসীকে বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলির একটি মনে করা হয়।
এই মন্দিরের নাম ছিল আদি বিশ্বেশ্বর মন্দির।
সেই মধ্যযূগ থেকে আমাদের দেশে পশ্চিম আর উত্তর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বহিরাগত মুসলমান আক্রমণ হয়েছে। সেই সব আক্রমণকারীরা কেউ এসেছে সোনা দানা লুট করতে, আবার কেউ এসেছে আমাদের দেশে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে। আমাদের ইতিহাস বইয়ের পাতায় খুললেই পড়া যায় শুধুসেই সব যুদ্ধের কাহিনী – সেখানে শুধু তলোয়ারের ঝনঝনানি, ঘোড়াদের হ্রেষা ধ্বনি, আর যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা হাজার হাজার রক্তাক্ত মৃতদেহ। এক দিকে আল্লা হু আকবর আর অন্যদিকে হর হর মহাদেব চিৎকার!
এই সব আক্রমণকারীদের নামের লম্বা লিস্ট। মহম্মদ ঘোরী থেকে শুরু করে ইলতুৎমিস, ফিরোজ শা তুঘলক, কুতুবউদ্দিন আইবক্ …
হিন্দু রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করার পর তাদের সৈন্যরা সারা দেশ জুড়ে একের পর এক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার জায়গায় মসজিদ স্থাপন করে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেও সেই সব মন্দিরের পুনর্নিমাণ হয়েছে, ধনী এবং ধর্ম্মভীরু হিন্দু রাজা বা বণিক বা জমিদাররা সু্যোগ পেলেই সেই কাজ করেছেন।
এই ভাবেই যুগে যুগে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরেরও ভাঙা গড়া চলে এসেছে।
ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট আকবরের সময়কাল ছিল বারাণসীর সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যুগ। আকবর শহরটিকে সাজিয়ে তোলেন। ১৫৮৫ সালে সম্রাট আকবর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং শিব ও বিষ্ণুর দুটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। পুণের রাজা সেই সময় অন্নপূর্ণা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় শের শাহ কলকাতা থেকে পেশোয়ার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করার পরে এই অঞ্চলের পরিবহন পরিকাঠামোরও উন্নতি ঘটেছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্যটকেরা আবার এই শহরে আসা শুরু করেন।
আবার ১৬৬৯ সালে আওরংজেব সম্রাট হবার পরেই পুনরায় মন্দিরটি ধ্বংস করে সেখানে জ্ঞানবাপী মসজিদ তৈরি করান। এই মসজিদটি আজও মন্দিরের পাশে অবস্থিত। ১৭০১ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ভেঙে পড়ে, এবং ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের শাসনভার হিন্দু সামন্ত রাজাদের হাতে চলে যায়। আধুনিক বারাণসীর বেশিরভাগটাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুত ও মারাঠা রাজাদের হাতে তৈরি।
১৭৩৭ সালে মুঘল সম্রাট কাশী রাজ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরে ব্রিটিশ যুগে কাশীর রাজাই এখানকার মুখ্য শাসক হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাশীর রাজবংশ বারাণসী শাসন করেছিল।
এর পরে আসে মারাঠা ও ব্রিটিশ আমল।
বর্তমান মন্দিরটি ১৭৮০ সালে মালহার রাও হোলকার এর পুত্রবধূ তথা হোলকার (আজকের ইন্দোর) রাজ্যের মহারানি অহল্যাবাই নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ভক্তিমতী ও সুশাসক হিসেবে রাণী অহল্যাবাই এর খুব সুনাম ছিল, তাঁর আমলে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়নি, প্রজারা শান্তিতে বসবাস করতো। তিনি বহু জনহিতকর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।
১৮৩৫ সালে পাঞ্জাবের শিখ সম্রাট রঞ্জিত সিংহ মন্দিরের চূড়াটি ১০০০ কিলোগ্রাম সোনা দিয়ে মুড়ে দেন।
আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ভিতর কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির একটি বহু আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে।
পশ্চিম এশিয়াতে জেরুসালেম এও মধ্যযুগে ধর্ম্মযুদ্ধে (crusade) ক্রীশ্চান আর মুসলমানদের এই গীর্জ্জা আর মসজিদ ভাঙা গড়া হয়েছে। ২০১৩ সালে যখন আমি জেরুসালেমে গিয়েছিলাম, তখন সেই ভাঙা গড়ার নিদর্শন আমি দেখেছি। সেখানে উনবিংশ শতাব্দীতে অটোমানদের রাজত্বের সময় (১৮৫০) একটা “ফিরমান” জারী করা হয়, তাতে দুই পক্ষই রাজী হয় যে এর পর থেকে আর কোন ভাঙা গড়া নয়, জেরুসালেম ও বেথেলহেমের সব গীর্জ্জা আর মসজিদই এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই থাকবে। এই ফিরমানের নাম ছিল “Status Quo”~
আমাদের দেশে অবশ্য এরকম কোন ফিরমান জারীর কোন প্রশ্ন ছিলনা, কেননা এখানে মুসলমান শাসকেরা এক তরফা হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করে গেছে। শোনা যায় যে কাশী শহরেই প্রায় ৩০,০০০ মন্দির ধ্বংস করা হয়, তার মধ্যে আদি বিশ্বেশ্বর মন্দির চত্বরে চল্লিশটি মন্দির ছিল।
মূল মন্দিরের উত্তর দিকে একটি পবিত্র কূপ আছে । প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে আক্রমণকারীদের হাত থেকে জ্যোতির্লিঙ্গ কে বাঁচাবার জন্যে এক পুরোহিত নাকি মূর্ত্তি নিয়ে এই কূপটিতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।
তবে ফিরমান না থাকলেও ব্রিটিশ আমল থেকেই আইন করে মন্দির মসজিদ ধ্বংস করার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পরে আমাদের নিজেদের সংবিধান তৈরী হয়, যেখানে পরিস্কার লেখা আছে যে আমরা একটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক (secular, democratic) দেশ – সুতরাং এখন আর কারুর মন্দির বা মসজিদ ধ্বংস করার কোন অধিকার নেই।
২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির (বি জে পি) হিন্দুত্ববাদী সরকার। তাদের উদ্যোগে যে সব হিন্দু মন্দির বহিরাগত মুসলমান শাসকেরা বিশেষ করে আওরঙ্গজেব – ভেঙে বা নিষ্ক্রিয় করে তার জায়গায় মসজিদ তৈরী করেছিলেন, সেই সব মসজিদ গুলো সব এক এক করে ভেঙে বা সরিয়ে তাদের জায়গায় ধ্বংস হওয়া মন্দিরগুলো আবার নতুন সাজে গড়ে উঠছে। প্রথমে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি তে বাবরী মসজিদ ভেঙে রামলালা (শিশু রামের) সরযু নদীর তীরে বিশাল বর্ণাঢ্য মন্দির তৈরী হলো, আর তার পরে সম্প্রতি কাশীতে জ্ঞানব্যাপী মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে নতুন বিশ্বনাথ এর মন্দির চালু হয়েছে। এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে বি জে পি কে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে অনুমতিও পেতে হয়েছে। বিশ্বনাথ মন্দিরের আশেপাশে চল্লিশটিরও বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত, শতাব্দী প্রাচীন মন্দির পাওয়া গেছে এবং তার প্রত্যেকটিই পুনর্নির্মিত হয়েছে।
জ্ঞানবাপী মসজিদ কে দূরে কোথাও সরিয়ে দেওয়া হবে আদালত থেকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর পরে মথুরায় বিষ্ণু মন্দির নতুন করে তৈরী করবার জন্যে আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা করা হচ্ছে।
বিশ্বনাথ দর্শন।
আজ সকাল দশটায় কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে আমাদের টিকিট কাটা আছে। তাই বিশ্বনাথ দর্শন আজকে আমাদের প্রথম কাজ।
আমার ছোটবেলায় কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে যাবার জন্যে একটা সরু গলি ছিল, তার নাম ছিল বিশ্বনাথের গলি। তার দুই পাশে দোকান আর নানা ছোট মন্দির ছিল, আর ছিল গিজগিজে ভীড়। নদী থেকে মন্দিরে প্রবেশ করার কোন ঘাট বা রাস্তা ছিলনা।
জায়গাটা ২০২২ সালের পরে আমূল পাল্টে গেছে।
আগের সেই বিশ্বনাথের সরু গলি আর নেই। ঠাসাঠাসি ভীড় ও নেই। সেখানে এখন বেশ চওড়া একটি রাস্তা। এখন মন্দিরের চত্বরটি বিশাল করা হয়েছে, সেই চত্বর এখন পরিস্কার ঝকঝকে সেখানে মার্বেলের সাদা মেঝে। ভীড় কমানোর জন্যে ইন্টারনেটে আগে থেকে টিকিট কেনার বন্দোবস্ত হয়েছে।
এখন Internet এ আগে থেকে পাস নিতে হয়, আমাদের তিন জনের পাস আজ সকাল দশটায়। এখন গলি দিয়ে না গিয়ে নদীর ঘাট থেকেও মন্দিরে ঢোকার বন্দোবস্ত হয়েছে। আমরা আগে বড় রাস্তার ধারে একটা দোকানে প্রসাদ আর পূজোর জিনিষ পত্র কিনে সেখানে চটি রেখে মন্দিরে ঢুকলাম।
বিশ্বনাথ মন্দিরের ভেতরে ঢুকে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। মার্বেল পাথরে বাঁধানো ঝকঝকে পরিস্কার বিশাল প্রাঙ্গন। সেই চত্বরে দেখা যায় অনেক ছোট ছোট মন্দির। মাঝখানে বিশ্বনাথের মন্দির, মাথার ওপরে সোনার চূড়া। সামনে ঢোকার জন্যে ছোট সুশৃঙ্খল লাইন। সময় অনুযায়ী ব্যাচে ভাগ করাতে কোনরকম বিশৃঙ্খলা নেই, আমাদের লাইনে মাত্র কুড়ি ত্রিশ জন পুরুষ নারী ও শিশু, প্রতেকের হাতে টিকিট। সেই টিকিট দেখার জন্যে একজন গার্ড মন্দিরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে।
সব মিলিয়ে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত। ভাল ভাবে দর্শন আর পূজো হলো। তার পরে গেলাম অন্নপূর্ণার মন্দির, এবং এক এক করে আরো অনেক মন্দির যা ওই বিশাল পাথরে বাঁধানো পরিস্কার চত্বরে ছড়িয়ে আছে।
মা’র কথা ভাবছিলাম। ভীড়ের মধ্যে কত কষ্ট করে দর্শন করতেন মা। খুব শিবে ভক্তি ছিল তাঁর।
শুধু মন্দির নয়। চত্বরের ভিতরে চারিপাশে লাইব্রেরী, ভি আই পি লাউঞ্জ, মিউজিয়াম, কনফারেন্স রুম, আরও কত কি! এলাহী ব্যাপার।
বেরোবার সময় দেখি আগাপাস্তলা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা জ্ঞানব্যাপী মসজিদ। কোন লোক নেই সেখানে, এখানে এখন আর কোন নমাজ পড়া হয়না। কিছু সিকিউরিটির লোক পাহারা দিচ্ছে যাতে কোন গোলমাল না হয়। হয়তো কিছুদিন পরে এই মসজিদ ভেঙে ফেলা হবে।
কালভৈরবের মন্দির
বিশ্বনাথ দর্শনের পর কিছুটা দূরে গিয়ে কালভৈরবের মন্দির। সরু গলির ভিতরে ঢুকতে হবে, তাই আমাদের অটো দূরে পার্ক করে রেখে আমরা কিছুটা হেঁটে দর্শন করে এলাম। তখন বেলা বারোটা হবে, গলিতে বেশ ভীড়, সবাই মন্দিরেই যাচ্ছে, গলির দুই পাশে অনেক দোকান, সেখানে কালভৈরবের ছবি সহ নানা পূজোর সামগ্রী বিক্রী হচ্ছে।
আমি কালভৈরবের মন্দিরে আগে আসিনি, এই প্রথম।
তবে বহু দিন আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “প্রথম আলো” উপন্যাস পড়ার সময় তাঁর নাম জেনেছিলাম। সেই উপন্যাসে এক জায়গায় ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রমানিক্য তাঁর সঙ্গী শশীভূষনের সাথে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এক জায়গায় গিয়ে একটি ভাঙ্গা মন্দির এবং তার পিছনে পাহাড়ের গায়ে একটি ছবি দেখতে পান্, তিনটি চোখ, আর পাশে একটি ত্রিশুল!
বীরচন্দ্র অবাক বিষ্ময়ে বলে ওঠেন – “কালভৈরব!”
জায়গাটার নাম উনকোটি অর্থাৎ এক কোটি থেকে এক কম। সেখানে নির্জন জঙ্গলে পাহাড়ের গায়ে নাকি শত সহস্র হিন্দু দেবদেবীর ছবি আর মূর্ত্তি রাখা আছে।
শুনলাম যেএই কাল ভৈরবের মন্দির কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আর কাশী এলে কালভৈরবকে একবার সব ভক্তই দর্শন করে পূজো দিয়ে যান্। আমরাও তাই করলাম।
এই কালভৈরব কিসের দেবতা?
হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, কাল ভৈরবের মন্দিরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন শিবের রুদ্র রূপের এক মূর্তি। এই মন্দিরের প্রধান দেবতা, ভগবান কাল ভৈরব, ভগবান শিবের ভয়ঙ্কর প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হয়। কাল ভৈরব হলেন শক্তির আধার। শিবের জ্বলন্ত প্রচণ্ড রূপকেই কাল ভৈরব হিসেবে ধরা হয়। তাঁকে বলা হয় কাশীর কোতওয়াল বা কাশীর রক্ষাকর্তা। হিন্দুদের বিশ্বাস, কালভৈরব প্রাচীন শহর বারাণসী ও শহরবাসীদেরও রক্ষা করেন।
হিন্দু পুরাণে বাবা কাল ভৈরবকে ঘিরে নানা কাহিনির উল্লেখ আছে। মনে করা হয়, তিনি হলেন মহাদেবেরই আর এক রূপ। কাল ভৈরবের মন্দিরে দর্শন করলে জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে প্রচলিত বিশ্বাস।
আমার মনে পড়ে ১৯৬২ সালে, তখন আমি স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি, চীনের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবার পরে জনসাধারণ কে অনুপ্রাণিত করার জন্যে রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের একটি গান প্রায়ই বাজানো হতো – “হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহো…”


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে পিন্ডদান
কালভৈরব মন্দির থেকে বেরিয়ে আমাদের আসল কাজ। ভারত সেবাশ্রমের মন্দিরে মা আর আমার শ্বাশুড়ীর পিণ্ডদান। বেলা বারোটায় সময় দেওয়া আছে, তার একটু আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম।
শহরের অপেক্ষাকৃত পরিস্কার জায়গায় বেশ চওড়া বড় রাস্তার ওপরেই ভারত সেবাশ্রমের মন্দির, আর থাকার জন্যে ধর্মশালা। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখলাম বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি বড় মন্দির, এবং ডান দিকে একটি তিনতলা বাড়ী, সেখানে মনে হলো একটি হোটেল বা ধর্ম্মশালা আছে, বেশ কিছু পরিবারকে সেখানে দেখলাম, কাশীতে এলে অনেকেই এখানে এসে ওঠেন। বিশেষ করে বাঙালীদের জন্যে এই ধর্ম্মশালা খুব জনপ্রিয়, বোধহয় শুদ্ধ নিরামিষ বাঙালী খাবার, পরিস্কার থাকার জায়গা, আর সস্তা বলেই।
আমাদের পুরোহিত ছোটু মহারাজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দুজনে একসাথে পিন্ডদানের পুজো করলাম। পুরোহিত ভদ্রলোক সব কেনাকাটা এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন।
বেশ নিষ্ঠার সাথে তিনি পূজো করলেন, মনে হলো এই কাজে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা। এক ঘন্টার মধ্যে আমাদের কাজ হয়ে গেল।
আমার মা আর আমার শ্বাশুড়ীর আত্মার শান্তি হোক। ওঁদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হলো পিন্ড পেতে। এক বছরের মধ্যে পিন্ড দেবার কথা, কিন্তু অবশ্য বাৎসরিক কাজ বাড়িতে করেছি এক বছর পরে। কিন্তু এখন তাঁদের আত্মার সদগতি হল, তাঁরা এখন নিশ্চিন্তে বৈতরনী পার করে স্বর্গে চলে গেছেন। সেখানে তাঁদের এখন অপার শান্তি।
মনে মনে একটা দৃশ্য কল্পনা করছিলাম, মা’র অশরীরী প্রেতাত্মা বৈতরণী পার হতেই দেখছেন, দিদা মামা মাসী বাবা এবং তাঁর অন্যান্য প্রিয়জনেদের প্রেতাত্মারা তার জন্যে নদীর ওপারে অপেক্ষা করছেন। কত দিন পরে আবার তাঁদের সাথে মা মিলিত হলেন।
ছোটু মহারাজ কে বিদায় জানাবার আগে তাঁর সাথে একটা ছবি তোলা হলো।


বাটি চোখা
এর পরে ছেলেটি আমাদের নিয়ে গেল “বাটি চোখা” নামে একটি দামী রেস্তোরাঁয়। কাশীতে এই রেস্তোঁরাটি নাকি খুব বিখ্যাত।
ডাইনিং রুম টা দোতলায়। ঢোকার পথে নীচে দেখি বেশ কিছু মহিলা ঘোমটা পরে ময়দা বেলছেন আর তরকারী কাটছেন। বেশ বড় রেস্তোরাঁ, আর বেশ ভীড় । মেনু হলো মোটা মোটা রুটির সাথে ডাল আর পাঁচমিশেলী তরকারী। গাইড ছেলেটিও খেলো আমাদের সাথে।
এই খাবারটা নাকি এখানে প্রচন্ড জনপ্রিয়। আমার অবশ্য খাবারটা তেমন কিছু ভাল লাগলোনা। বেশ অখাদ্যই বলা যায়। এত মোটা রুটি আর ডাল তার সাথে কিছুটা বিস্বাদ তরকারী – অন্ততঃ আমার কাছে – কে আর ভালবেসে খায়?
শেষ পাতে অবশ্য উত্তর ভারতের মিষ্টি – বরফি, লাড্ডু, কালাকাঁদ, ইত্যাদি ছিল, সাথে মিষ্টি লস্যি।
বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি
লাঞ্চের পরে আমরা গেলাম BHU ক্যাম্পাস দেখতে। তখন বেলা প্রায় তিনটে।
একটা তো মাত্র দিন তার মধ্যে যতোটা পারি ঘুরে দেখা।
বেশ বড় আর সুন্দর সবুজ গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা সুন্দর BHU ক্যাম্পাস, এখন তার একটা ভাগ IIT হয়েছে। কিন্তু যেহেতু একবারে শহরের মাঝখানে, তাই ক্যাম্পাসের ভিতর যেন শান্তি ও নীরবতার কিছুটা অভাব। সাইকেল রিক্সা আর বাস চলছে ক্যাম্পাসের রাস্তা দিয়ে। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে কিছু লোক।
ছাত্রাবাসগুলো রাস্তার ধারে।
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশ বাহিনী এখানে একদল বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাকে হত্যা করে। থিওসফির প্রচারে অ্যানি বেসান্ত এখানে এসেছিলেন। “সকল ধর্মের মানুষকে একই ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধের প্রচার ভারতবাসীর মন থেকে সকল কুপ্রথা দূর করতে” তিনি এখানে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। ১৯১৬ সালে এই কলেজটি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।
আমাদের দেশের এটি একটি প্রধান এবং স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়, এখান থেকে আমার মামা স্বর্গীয় ধ্রুবনারায়াণ বাগচী ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছিলেন। পরে আমার মামাতো ভাই ভাস্বর ও তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখান থেকেই ইঞ্জিনীয়ারিং এ গ্রাজুয়েশন করে। আমার বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে।
সঙ্কটমোচন মন্দির
ক্যাম্পাসে ঘুরে আমরা গেলাম সঙ্কটমোচন – হনুমানের মন্দিরে।
ভারত ও ভারতের বাইরে হনুমান মন্দির আছে অসংখ্য, তবে কাশীধামের এই সংকটমোচন মন্দিরটি সবচেয়ে জাগ্রত বলে পরিচিত। হনুমানজী কাশীর এই মন্দিরে অবস্থান করে ভক্তদের জীবনের নানা সঙ্কট থেকে মুক্ত করেন।
অনেকটা জায়গা নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গনের ভিতরে অনেক বড় বড় গাছ, ঢুকতেই বাঁ পাশে সংকটমোচন, আর ডানদিকে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। মন্দির দু’টি মুখোমুখি। ভাবটা এমন, রাম ছাড়া হনুমান চলবে না। হনুমান ছাড়া রামের এক পা যাওয়ার জো নেই।
হনুমানজীর মন্দিরে হনুমান থাকবেনা তা তো আর হয়না। দেখি প্রকান্ড ল্যাজ ঝুলিয়ে ডালে ডালে বসে আছে অনেক মুখপোড়া হনুমান। কাউকে প্রসাদ দিতে দেখলই তারা দল বেঁধে গাছ থেকে নেমে আসে। তাদের বেশ আগ্রাসী মনোভাব।
সংকটমোচন মন্দিরে সিঁদুর রাঙানো হনুমানজি ছাড়াও আছে বিশ্বনাথ মহাদেবের একটি লিঙ্গ বিগ্রহ। বিপরীতে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মীজির সুসজ্জিত বিগ্রহ।
মন্দিরের সামনে ভীড় আর লম্বা লাইন। মাঝে মাঝেই ভক্তদের জোর গলায় আওয়াজ ভেসে আসছে “ভারত মাতা কি জয়!”
বেনারসী শাড়ী
এর পরে বেনারসী শাড়ী কেনা।
গাইড ছেলেটি আমাদের নিয়ে গেল একটি গলির মধ্যে এক বিরাট শাড়ীর আড়তে। সেখানে দোতলায় মাটিতে বসে চারিদিকে শাড়ী বিছিয়ে আমাদের শাড়ী দেখালেন এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক – তাঁর চোখে মুখে কথা। চমৎকার ব্যক্তিত্ব, রসিক মানুষ, খদ্দের কে বাগে আনার অসীম ক্ষমতা। তিনি দোকানের ম্যানেজার না মালিক ঠিক বোঝা গেলনা। কিন্তু সেলসম্যান হিসেবে দুর্দ্দান্ত। এঁর কাছে এসে কিছু না কিনে ফেরা প্রায় অসম্ভব।
তিন খানা দামী শাড়ী তিনি অবলীলায় গছিয়ে দিলেন আমাদের।
অবশ্য আমাদের তো তিনটেই দরকার ছিল। দুই মেয়ে আর সুভদ্রা। ভালোই হলো ওরা পছন্দ করে কিনলো। সামনে আমাদের বিয়ের সুবর্ণবার্ষিকী, সেই অনুষ্ঠানে মেয়েরা দু’জন এই বেনারসী শাড়ী পরবে।
আমার ছোটবেলায় বিশ্বনাথের গলির মোড়ে অনেক বেনারসী শাড়ীর দোকান ছিল, আমার মনে পড়ে একবার ছোড়দাদুর (দিদার ছোট ভাই দূর্গাপ্রসন্ন আচার্য্য, মা’র ছোটমামা) বড় মেয়ে রমা মাসীর বিয়ের বেনারসী কেনার ভার পড়েছিল মা’র ওপর। অনেক দোকান ঘুরে অনেক বাছাবাছি করে মা একটা বেশ দামী লাল বেনারসী পছন্দ করেছিলেন।
আমার ছোটবেলার কাশীর স্মৃতির মধ্যে বিশ্বনাথের গলিতে বেনারসী শাড়ীর দোকানে এক গাদা শাড়ীর পাহাড়, তার মধ্যে মা শাড়ী বেছে যাচ্ছেন, আমি পাশে বসে, আমার বয়েসী খুব মিষ্টি দেখতে একটি ছোট্ট মেয়ে – সম্ভবতঃ দোকানদারের মেয়ে – বিনুনী করে পরিপাটি চুল বাঁধা, একটা লাল ডুরে শাড়ি পরে এক পাশে বসে চুপ করে মা’র শাড়ী বাছা দেখতো, তাকেও ভুলিনি।




রাবড়ী, পান, আর সান্ধ্য নৌকাভ্রমণ
শাড়ী কিনে হোটেল ফেরার পথে বেনারসের বিখ্যাত রাবড়ী আর পান না খেলে কি করে হয়?
শেষে হোটেলে যখন পৌছলাম, তখনও বাইরে দিনের আলো। ঘরের পাশে বারান্দায় সামনে নদী দেখতে দেখতে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজও একটা নৌকা ভ্রমণ হলো। প্রায় রেল ব্রীজ পর্য্যন্ত চলে গেলাম আজ। তার পর মণিকর্ণিকা আর হরিশচন্দ্র ঘাটের শ্মশান দেখে অসি ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরলাম।
আজও রাত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে আর অসি ঘাটে গঙ্গারতি হচ্ছে দেখলাম, নদীর জলে আর ঢেউতে সেই আরতির আলোর ছায়া কাঁপছে।
দেখতে বেশ লাগছিল।
এবার মাত্র এক দিনের জন্যে কাশী এসেছিলাম আমরা। বড্ডই কম সময়। আর একটা দিন বেশী থাকলে আমরা সারনাথ আর রামনগরে কাশীর রাজার (নরেশ) প্রাসাদ আর দূর্গ দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু এই ভাবেই এই ট্রিপ টা প্ল্যান করেছিলাম, তাই এখন আর কিছু করার নেই। পুপুকেও লন্ডনে ফিরতে হবে, তার ছুটি কম, ফেরার টিকিট ও কাটা হয়ে গেছে। কালকে দুপুরে আমাদের কলকাতার ফ্লাইট, পুপু আর আমি ঠিক করলাম যে ভোরবেলা দু’জনে মিলে নদীর ধার ধরে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত হাঁটবো।






৫) তৃতীয় এবং শেষ দিন
আজ আমাদের ফেরা। ব্রেকফাস্টের পরে হোটেল থেকে চেক আউট করে এয়ারপোর্ট।
তার আগে কথামতো ভোরবেলা আমি আর পুপু ঘুম থেকে উঠে একটু নীচে নদীর ধারে হেঁটে এলাম। একটার পর একটা ঘাট পেরিয়ে যাচ্ছি, নদীর ধারে লোকের ভীড় বাড়ছে, কিছু কিছু জায়গায় পূজোয় বসেছে পুরোহিতেরা, তাদের যজমানেরা তাদের ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। অনেকের খালি গায়ে পৈতে, অনেকের মাথা ন্যাড়া। সবাই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু। নদীর পাড়ে প্রায়ই চোখে পড়ছে লাল রং এর শিব মন্দির, আর মন্দিরের পাশে বট বা অশ্বথ গাছ, তাদের ডালে বাঁদরের দল।
“নৌকা চড়বেন বাবু?” বলে অনেক বোটের চালকরা এসে আমাদের ধরছে। নদীতে অনেক মাছধরা নৌকা। মাছের লোভে তাদের পিছন পিছন উড়ে যাচ্ছে সাদা সারস পাখীরা।
অনেকটা দূর হেঁটেছিলাম আমরা দু’জন সেদিন।
হরিশ্চন্দ্র আর মণিকর্ণিকা ঘাটে চিতাকাঠের স্তুপ রাখা। জ্বলন্ত চিতার ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস কিছুটা বন্ধ হয়ে আসে। মৃতের আত্মীয়রা এবং প্রিয়জনেরা মুখ ম্লান করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।
ঘাটের পাশে উঁচু উঁচু লাল রং এর সব বড় বড় বাড়ী। অনেক দূরে কিছুটা ছায়ায় ঢাকা রেল ব্রীজ। নদীর ওপারে চর, সেখানে গাছপালার মাঝে কিছু ঘরও চোখে পড়ে। ওই চরেও মানুষ বাস করে? কি জানি, হবেও বা।
সেদিন সকালে পুপুর সাথে কাশীর ঘাটে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় মনে পড়ে যাচ্ছিল ছোটবেলায় আমি আর আমার সমবয়েসী মাসতুতো ভাই রঞ্জু এরকম সারাদিন কাশীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াতাম।
একবার ছিলাম শুধু আমি আর মা। সেদিন বোধহয় মাসীরা সবাই ফিরে গেছেন, বাড়ীতে শুধু আমি আর মা। আমরাও পরের দিন ট্রেণ ধরে ফিরে যাবো। তাই আমাদের মন খারাপ।
মা বললেন চল্ মান্টু আমরা দু’জন নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি। সাধারণতঃ কাশীতে গেলে আমি মা’কে কখনো একা পেতামনা। আশে পাশে অনেকে থাকতো, দিদা, মাসীরা। তাছাড়া মা’র মধ্যে ভালবাসার প্রকাশ তেমন ছিলনা। জড়িয়ে ধরা বা মাথায় হাত বোলানো, বা আদর করা, এই সব মা’র স্বভাবে ছিলনা। বরং কারণে অকারণে তাঁর শাসনেই আমি বেশী অভ্যস্ত ছিলাম।
এখনো মা’র সঙ্গে কাটানো সেই পড়ন্ত সন্ধ্যয় কাশীর গঙ্গার ঘাটে হাঁটার কথা মনে পড়ে। বোধ হয় চৌষট্টি ঘাট থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত হেঁটেছিলাম আমরা দু’জন। কিছু কি কথা হচ্ছিল আমাদের মা আর ছেলের মধ্যে? দুজনের পৃথিবী আলাদা, দুজনেই হয়তো নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম।
সেদিন আমার জন্যে একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ অপেক্ষা করে ছিল।
ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি লোক গুড় আর বাদামের মিষ্টি চাকতি বিক্রী করছিল। আমার বোধ হয় একটু লোভ হয়ে থাকবে, কিন্তু আমি না চাইতেও মা আমায় একটা চাকতি কিনে দিয়েছিলেন। কি জানি হয়তো লোভী চোখে তাকিয়েছিলাম, মা লক্ষ্য করে থাকবেন। বেশী দাম ছিলনা, এক আনা বা দুই আনা হবে, কিন্তু সেই যুগে হয়তো অনেক। ছোটবেলায় ওই সব খাবার খুব প্রিয় হয়, নিজে কিনে খাবার তো সুযোগ ছিলনা, সেই জন্যেই হয়তো।
খুব ভাল লেগেছিল মনে পড়ে। আবার একটু হালকা অস্বস্তিও হয়েছিল, কেননা ওই বয়সেও আমি জানতাম আমরা গরীব, জীবিকার জন্যে মা’কে চাকরী করতে হয়, মা’র কাছে হয়তো এটা একটা বাজে খরচ, তাছাড়া রাস্তার জিনিষ কিনে খাওয়াও তো মা পছন্দ করেননা।
কিন্তু আজ নিজে থেকেই …
মা’র কাছ থেকে তাঁর এরকম অপ্রকাশ্য অন্তঃসলিলা ভালবাসা পাবার আরও অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, কিন্তু কাশীর ঘাটে সেই সন্ধ্যায় আমায় বাদামের চাকতি কিনে দেবার ঘটনাটা এই জন্যে এখানে লিখলাম যে এতদিন পরে বার্দ্ধক্যে পৌঁছে কাশীর ঘাটে এখন আমি আর আমার মেয়ে পুপু। সে এখন আমার জীবনে আমার মা’র জায়গাটা নিয়ে ফেলেছে। আমার মা’র মতোই আমার প্রতি তার অকৃত্রিম আর শর্ত্তহীন ভালবাসা। তবে সেই ভালবাসা আর তার দুশ্চিন্তা অবশ্য অনেক বেশী প্রকাশ্য।
যাই হোক, দু’জনে মিলে অনেকটা হাঁটলাম সেদিন ভোরে। হোটেলে ফিরে এসে স্নান সেরে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে চেক আউট করে বেরিয়ে পড়লাম।
হোটেলের লোকেরা আমাদের মাল পৌঁছে দিল বড় রাস্তায়, সেখানে তার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল ভোলা। সে আমাদের পোঁছে দিল কাশী এয়ারপোর্টে।





হোটেলের দুই কর্মচারী আর ড্রাইভার ভোলার সাথে ফেরার দিন